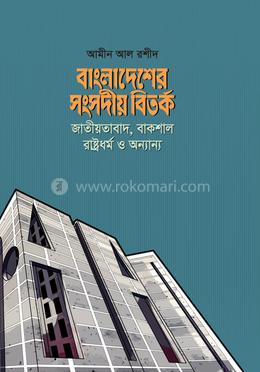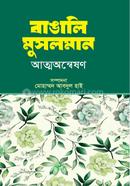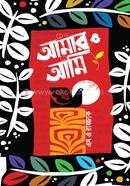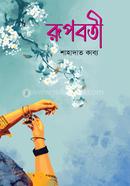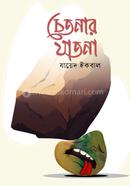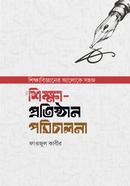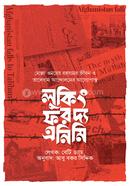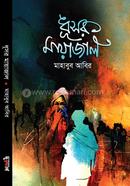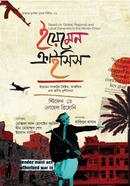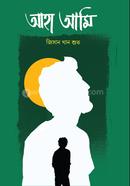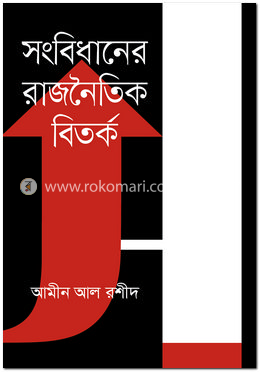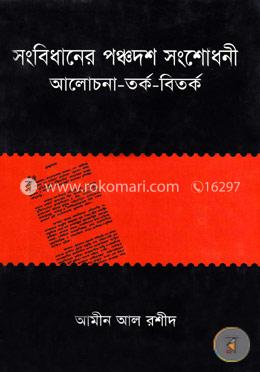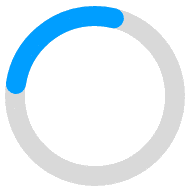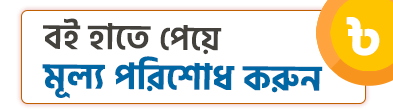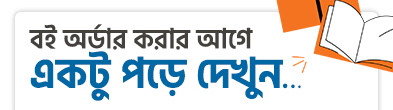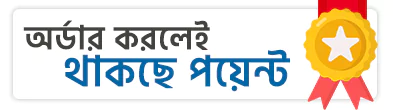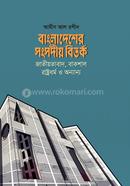কেন এই বই
রাষ্ট্র্র্র পরিচালনায় বিশ্বজুড়ে যত মত আছে, নানা সীমাবদ্ধতার পরেও এখন পর্যন্ত গণতন্ত্রই তুলনামূলকভাবে উত্তমÑএ বিষয়ে আপনি হয়তো দ্বিমত করবেন না। আর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সংসদ (এককক্ষ বা দ্বিকক্ষ) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মÑযা সরকারকে জবাবদিহির মধ্যে রাখতে পারে। সরকারের অপরাপর অঙ্গ ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যাতে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় থাকে, সেরকম আইনি কাঠামো গড়ে তোলার জন্যও সংসদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।
স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল সংসদীয় গণতন্ত্রের হাত ধরেই। যদিও বছর কয়েকের মধ্যে সেখানে ছন্দপতন ঘটে। আসে একদলীয় শাসনব্যবস্থা। গুরুত্বহীন হয়ে যায় জাতীয় সংসদ। এরপর একাধিকবার ‘বন্দুকের শাসন’। সেই অবস্থার অবসান হয় ১৯৯১ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এবং দেশ নতুন করে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার দিকে যাত্রা করে। বস্তুত ১৯৯১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দেশের রাজনীতি ও সংসদীয় ব্যবস্থায় একটা মোটামুটি ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় ছিল। কিন্তু এরপরেই আসে আরেক পরোক্ষ বন্দুকের শাসনÑযেটি ‘ওয়ান ইলেভেন’ বা ‘এক-এগারোর সরকার’ নামে পরিচিত। অফিসিয়ালি তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলেও এটি ছিল মূলত ‘সেনা নিয়ন্ত্রিত সুশীল সরকার’।
এই সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ আসনে জয় পেয়ে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ এবং ওই সংসদেই তারা নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান বাতিল করে সংবিধান সংশোধন করে। এর ফলে পরবর্তী তিনটি নির্বাচন (২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪) আওয়ামী লীগ নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে করে। যার ফলে প্রতিটি নির্বাচনের পরে তারা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে। এই নির্বাচনগুলো দেশে-বিদেশে নানা সমালোচনার জন্ম দেয়। যদিও ২০২৪ সালের নির্বাচনের পরে সরকার গঠন করলেও আওয়ামী লীগ সাত মাসের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। গণঅভ্যুত্থানের মুখে তাদের পতন হয় ওই বছরেরই ৫ আগস্ট। এরপর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকারÑযেটি আগের মতো তত্ত্বাবধায়ক সরকার নয়। কেননা যখন এই সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান ছিল না। ফলে তারা ‘স্টেট নেসেসিটি’র আলোকে সংবিধান সমুন্নত রেখেই এরকম একটি আপৎকালীন সরকার গঠন করে।
২.
বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের বয়স ৫০ বছরের বেশি হলেও এখানে কোনো ধারাবাহিকতা ছিল না। দীর্ঘ সময় সংসদ থাকলেও সেখানে সংসদীয় গণতন্ত্রের কোনো চর্চা ছিল না। বরং সংসদ ছিল এককেন্দ্রিক। ক্ষমতাসীনরা যেকোনো আইন বিনা বাধায় পাস করতে যেমন পেরেছে, তেমনি নিজেদের প্রয়োজনে সংবিধানও সংশোধন করেছে।
১৯৯১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত সময়কালেই বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের মোটামুটি চর্চা হয়েছে বলে ধরা হয়। ২০০৯ থেকে ২০১৪ সময়কালে সংসদে বিএনপি প্রধান বিরোধী দল হিসেবে থাকলেও সংখ্যায় তারা ছিল নগণ্য। যে কারণে ওই অর্থে সংসদ খুব প্রাণবন্ত ছিল না। কেননা সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্য সংখ্যায় ভারসাম্য না থাকলেও সরকারি দল নিজেদের ইচ্ছামতো যেকোনো আইন পাস করিয়ে নিতে পারে।
বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে অদ্ভুত সময়কাল ধরা হয় দশম ও একাদশ সংসদকে। বিশেষ করে দশম সংসদে বিরোধী দল জাতীয় পার্টি যে ধরনের ভূমিকা পালন করেছে, তাতে তাদেরকে ‘সরকারি বিরোধী দল’ বললেও অত্যুক্তি হয় না। একাদশ সংসদে বিএনপি নামমাত্র ছিল। যদিও পরে তাদের এমপিরা পদত্যাগ করেন। এরপর দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেয়নি।
৩.
বাংলাদেশের সংসদে গণতন্ত্রের চর্চা কতটুকু হয়েছে, সেটি বরাবরই প্রশ্নসাপেক্ষ। কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতার ভেতরেও সংসদে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে যে আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছেÑতা সংশ্লিষ্ট সংসদের কার্যকারিতা এবং ওই সময়ের জনপ্রতিনিধিদের স্ট্যান্ডার্ড বুঝতে কিছুটা হলেও সহায়ক। সেরকমই কয়েকটি ইস্যু বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সংসদ সদস্যদের পদ বাতিলসম্পর্কিত সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ, ব্যক্তির সম্পত্তি অর্জনের সীমারেখা, একদলীয় শাসনব্যবস্থা ‘বাকশাল’, রাষ্ট্র্র্রধর্ম, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ন্যায়পাল ইত্যাদি। এর বাইরে বাহাত্তরের মূল সংবিধানে ফিরে যাওয়ার চেষ্টায় পঞ্চদশ সংশোধনী; বিচারকদের অপসারণের বিধানসংবলিত সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ ইস্যুতে ষোড়শ সংশোধনীর পূর্বাপর এবং সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে দেশছাড়া করা নিয়েও সংসদের ভেতরে-বাইরে নানা আলোচনা হয়েছে। জনপরিসরে তো বটেই।
সবশেষ দ্বাদশ সংসদে আওয়ামী লীগের সাবেক সিনিয়র নেতা আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীর ‘বড়শিতত্ত্ব’ নিয়েও বেশ আলোচনা হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচিত আইনজীবী ব্যারিস্টার সায়েদুল হক সুমনও এই সংসদে কিছুদিন বিতর্ক করার চেষ্টা করেছেন। এসব বিষয়ে ঘটনার বিশ্লেষণ এবং সংসদ সাংবাদিক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করার সুবাদে কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার জন্য এই বই।
এই বইটি লেখার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের সংসদীয় বিতর্কের ধরন সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার পাশাপাশি আমাদের সংসদ কতটা কার্যকর, সেটি বোঝার চেষ্টা করা। সংসদীয় গণতন্ত্রের যে চর্চার মধ্যে বাংলাদেশ শুরু থেকেই কমবেশি আছে, সেখানের বিচ্যুতিগুলোও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে সংবিধানের যেসব বড়ো পরিবর্তন দেশের সরকার কাঠামো বদলে দেওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক সংকট জটিলতর করেছে, সেই সংশোধনীগুলো পাসের প্রক্রিয়ায় সংসদে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিলÑসাধারণ পাঠকের সে বিষয়ে আগ্রহ আছে নিশ্চয়ই। বিশেষ করে একজন জাতীয়তাবাদী ও গণতন্ত্রমনা নেতা হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু কেন বাকশাল কায়েমের মধ্য দিয়ে দেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু করলেন এবং এর প্রক্রিয়াটি কী ছিল; সংবিধান প্রণয়নের সময় গণপরিষদে বাঙালি জাতীয়তাবাদ নিয়ে কী ধরনের বির্তক হয়েছিল এবং কেন এই বিধানটি যুক্ত করা হলো; সংবিধানে রাষ্ট্র্র্রধর্মের বিধান যুক্ত করার যুক্তিগুলো কী ছিল এবং এই ঘটনাটি পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিকে কতটা প্রভাবিত করেছে; কোন প্রক্রিয়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে দেওয়া হলো এবং এই বিরাট সিদ্ধান্তটি নেওয়ার পেছনের ঘটনাগুলো কীÑতার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তা পাঠককে জানানোর তাগিদ থেকেই এই বইটি লেখা।
বইতে মোট অধ্যায় ১৫টি। এর মধ্যে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে সংসদে সংসদ সদস্যদের কথা বলার স্বাধীনতা খর্ব করে বলে যে অভিযোগ রয়েছে তার ভীতি ও বাস্তবতা; ন্যায়পাল ইস্যুতে আইন হলেও সেটি কার্যকর না হওয়া; দ্বাদশ সংসদে বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীর ‘বড়শিতত্ত্ব’ এবং জাতীয় পার্টির এমপি মুজিবুল হক চুন্নু ও আলোচিত এমপি ব্যারিস্টার সায়েদুল হক সুমনের বাহাস নিয়েও আলাদা অধ্যায় রয়েছে। এছাড়া ব্যক্তির সম্পত্তি অর্জনের সীমারেখা, বাহাত্তরের মূল সংবিধানে ফিরে যাওয়ার চেষ্টায় পঞ্চদশ সংশোধনী, সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার দেশত্যাগসহ নানা বিষয়ের ফ্যাক্ট ও বিশ্লেষণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
পাঠকের সুবিধার্থে বইয়ের শেষ অংশে সাময়িক সংবিধান আদেশ, ওয়েস্টমিনস্টার টাইপের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার পরিচিতি, গণপরিষদ, সংবিধান প্রণয়ন কমিটি এবং ৬ সদস্যের নোট অব ডিসেন্টও টিকা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে দুই মলাটের ভেতরে পাঠক আশা করি বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরুর পর থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কেসস্টাডিগুলোর ব্যাপারে একটা মোটামুটি ধারণা পাবেন। সংসদ সম্পর্কে আগ্রহী পাঠক তো বটেই, গবেষকদেরও চিন্তার খোরাক হতে পারে এই বই।
আমীন আল রশীদ
ফেব্রুয়ারি ২০২৫
প্রথম অধ্যায়
বাঙালি জাতীয়তাবাদ নিয়ে
গণপরিষদে তোলপাড়
রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যেদিন (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) দেশে ফিরলেন, তার পরদিনই তিনি সাময়িক সংবিধান আদেশ বলে রাষ্ট্র্র্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে ওয়েস্টমিনেস্টার টাইপের সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ নেন। এই প্রক্রিয়াগত পরিবর্তনের পেছনে যুক্তি দেখানো হয় যে, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছিল বাংলাদেশের জনগণের আকাক্সক্ষা এবং এই আকাক্সক্ষা বাস্তবায়নের জন্যই উক্ত আদেশ জারি করা হয়েছে। (মওদুদ আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, ইউপিএল/১৯৮৩, পৃ. ১১)।
সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মূল শর্ত ও সৌন্দর্যই হলো সংসদীয় বিতর্ক। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও সংখ্যালঘিষ্ঠ, এমনকি বিরোধী দলের চেয়ারে যদি একজন মাত্র সদস্যও উপবিষ্ট থাকেন, তাকেও যথেষ্ট পরিমাণে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়Ñ যার উদাহরণ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের সংসদের যাত্রা শুরুর আগেই ১৯৭২ সালে গঠিত ‘গণপরিষদ’। যে পরিষদ নতুন রাষ্ট্রের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করেছিল।
প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের গত ৫২ বছরের সংসদীয় ব্যবস্থায় সংসদ সদস্যদের কথা বলার স্বাধীনতায় অগ্রগতি কতটুকু? ১৯৭২ সালে গণপরিষদে কী ধরনের বিতর্ক হয়েছে? এর পরবর্তী সংসদগুলোয় কতটা প্রাণবন্ত বিতর্ক হয়েছে আর সাম্প্রতিক ইতিহাস কী বলছে?
সংসদীয় বিতর্ক
রাষ্ট্র্র্রপতির ভাষণ, জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়, উত্থাপিত কোনো প্রস্তাব বা বিলের ওপর সংসদ সদস্যদের মধ্যে যে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হয়, সেটিকেই সংসদীয় বিতর্ক বলা হয়। এই বিতর্কে সদস্যরা নিজ নিজ বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি ও অন্যের বক্তব্যের জবাবে পালটা যুক্তি তুলে ধরেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এই বিতর্ক পার্লামেন্টকে স্বচ্ছতা দান করে।
পার্লামেন্টে বিতর্কের যেমন সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে, তেমনি আছে নির্ধারিত সময়। বিতর্কের পরিণতিতে বিষয়টি ভোটে দেওয়া না-দেওয়া অথবা প্রস্তাব গ্রহণ বর্জনও হয়। সকল সদস্যকে সংসদ পরিচালনার গাইডলাইন কার্যপ্রণালি বিধি মেনে বিতর্কে অংশ নিতে হয়। এজন্য স্পিকারের অনুমতি নিতে হয়। একই সময় একাধিক সদস্য বক্তব্য রাখতে চাইলে স্পিকার যিনি আগে আগ্রহ দেখিয়েছেন তাকে সুযোগ দেন। বিতর্কের সময় স্পিকারকে সম্বোধন করে (মাননীয় স্পিকার বা ঐড়হড়ৎধনষব ঝঢ়বধশবৎ বলে) বক্তব্য রাখতে হয়। (জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্টারি শব্দকোষ, বাংলা একাডেমি/২০১০, পৃ. ৬৪)।
সংসদে কথা বলার স্বাধীনতা
সংসদে কথা বলার স্বাধীনতা সদস্যদের একটি বিশেষাধিকার। উপমহাদেশে এই স্বাধীনতা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। ব্রিটিশ-ভারতে প্রবর্তিত ১৯১৯ সালের ভারত শাসন বা মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনেও সংসদে সদস্যদের ইচ্ছে মতো কথা বলার স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সংবিধানের ৭৮(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: ‘সংসদে বা সংসদের কোনো কমিটিতে কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোনো সংসদ-সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।’
অর্থাৎ সংসদে একজন সদস্য যেকোনো বিষয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে স্বাধীন। তার ওই বক্তব্য নিয়ে সমালোচনার সুযোগ থাকলেও সংসদে দেওয়া বক্তব্যের কারণে কোনো সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা করার সুযোগ নেই। অথচ ওই একই বক্তব্য সংসদের বাইরে দিলে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন। এটিই হচ্ছে সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার বা প্রিভিলেজ। তবে সংসদে কথা বলার এই অবারিত স্বাধীনতা থাকা মানেই সংসদ সদস্যরা যা খুশি বলেন বা বলবেন, বিষয়টি এমন নয়। আইন ও সংবিধানে যাই বলা হোক না কেন, নীতি-নৈতিকতা ও রেওয়াজ মেনেই সদস্যরা কথা বলেন। তারা চাইলেই যা খুশি বলতে পারেন না। সেজন্য তাদেরকে সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি মানতে হয়।
একজন সদস্যের কথা বলার স্বাধীনতা আছে মানে তিনি সংসদে যা খুশি বলতে পারেন কি না, এই প্রশ্নে ভারতে বিতর্ক উঠলে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সংসদে সদস্যের ইচ্ছামতো কথা বলার স্বাধীনতা সংরক্ষিত থাকে। সদস্যের সংসদে বলা কথা বা তার দেওয়া ভোট নিয়ে কোনো আদালত কোনো কার্যধারা সৃষ্টি করতে পারবে না বলে আদালত রায় দেন। তবে আদালত এও বলেন যে, সদস্যদের কথা বলার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত হবে সংবিধানের নির্দেশ, কার্যপ্রণালি বিধি ও স্পিকারের কর্তৃত্ব দ্বারা। অর্থাৎ আদালত সদস্যদের বাক্স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতে না পারলেও সংসদীয় রীতিনীতি, সদস্যের ব্যক্তিগত বিবেচনা বোধ, স্পিকারের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং সংসদীয় কার্যপ্রণালি বিধি তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। (পার্লামেন্টারি শব্দকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫)।
গণপরিষদে সুরঞ্জিতের স্বাধীনতা
সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় একমাত্র বিরোধীদলীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত একাই প্রচুর কথা বলেছেন। সংবিধানের প্রতিটি অনুচ্ছেদ নিয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বেশি সময় পাচ্ছেন বলে কোনো কোনো সদস্য স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পরিষদের উপনেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯৭২ সালের ২৩ অক্টোবর গণপরিষদে বলেন, ‘সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত একটি বিশিষ্ট দলের বিশিষ্ট সদস্য এবং একমাত্র পার্লামেন্টারি সদস্য। সেই হিসেবে তাকে তার দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বক্তব্য পেশ করার জন্য স্পিকার যে সুযোগ দিয়েছেন, এতে আপত্তি করার কোনো কারণ নেই। কেননা একমাত্র বিরোধীদলীয় সদস্য হিসেবে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত একটু বেশি সময় পেতেই পারেন।’ (ব্যারিস্টার আব্দুল হালিম, গণপরিষদ বিতর্ক, সিসিবি ফাউন্ডেশন/২০১৪, পৃ. ১৬৯)।
গণপরিষদে সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের এই বাড়তি সময় পাওয়া বা দীর্ঘ বক্তৃতার প্রসঙ্গে বরেণ্য শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামান লিখেছেন, ‘সংবিধান বিলের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ নিয়ে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বেশ দীর্ঘ ও তীব্র বক্তৃতা দিতেন। বঙ্গবন্ধু একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি সুরঞ্জিতের বক্তব্য শুনছি কি না। বললাম, মাঝে মাঝে শুনি। তিনি হেসে বললেন, ‘১৯৫৬ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে কনস্টিটিউশন নিয়ে আমি যেসব কথা বলেছি, সেসব কথাই এখন সুরঞ্জিত আমাকে শোনাচ্ছে। তখনকার হাউজের ডিবেট পড়ে দেখো।’ (আনিসুজ্জামান, বিপুলা পৃথিবী, প্রথমা/২০১৫, পৃ. ৬০)।
তার মানে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সংবিধানের খসড়ার ওপরে যে দীর্ঘ ও ‘তীব্র’ বক্তৃতা দিতেন, তাতে স্বয়ং বঙ্গবন্ধুরও সায় ছিল।
প্রসঙ্গত, সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য গঠিত ৩৪ সদস্যের কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ভিন্নমতসূচক মন্তব্য বা নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছেন। শুধু তিনি একা নন, এই কমিটির আরও পাঁচজন সদস্য সংবিধানের ওপর এই নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় গণপরিষদ সদস্যরা কথা বলা ও মত প্রকাশের ক্ষেত্রে কতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করেছেন এবং তাদের কথার কতটুকু মূল্যায়ন হয়েছে, তা নিয়ে বিতর্ক আছে।
লারমা ও ‘বাঙালি’ বিতর্ক
সংবিধানের খসড়ায় ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে ছিল: বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে। কিন্তু সংবিধান বিলের ওপর দফাওয়ারি আলোচনায় ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর ঢাকা-১২ আসন থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য মো. আব্দুর রাজ্জাক ভূঁইয়া এই অনুচ্ছেদে একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনে বলেন, ‘বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে; বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।’
এ সময় স্পিকার মুহম্মদুল্লাহ প্রস্তাবটির বিষয়ে পরিষদ সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আইন ও সংসদীয় বিষয়াবলি এবং সংবিধান-প্রণয়ন-মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন বলেন, ‘মাননীয় স্পিকার সাহেব, এই সংশোধনী গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি এবং এটা গ্রহণ করা যেতে পারে।’
কিন্তু এর বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তিনি স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ‘আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙালিদের সঙ্গে আমরা লেখাপড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। সবদিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষÑ কেউ বলেন নাই, আমি বাঙালি। আমার সদস্য-সদস্যা ভাইবোনদের কাছে আমার আবেদন, আমি জানি না, আজ আমাদের এই সংবিধানে আমাদেরকে কেন বাঙালি বলে পরিচিত করতে চায়’...
লারমার কথা শেষ না হতেই স্পিকার তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘আপনি কি বাঙালি হতে চান না?’
উত্তরে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেন, ‘আমাদিগকে বাঙালি জাতি বলে কখনও বলা হয় নাই। আমরা কোনোদিনই নিজেদেরকে বাঙালি বলে মনে করি নাই। আজ যদি এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানের জন্য এই সংশোধনী পাস হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এই চাকমা জাতির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশি বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙালি বলে নয়।’
এটুকু বলার পরে স্পিকার তাকে বসতে বলেন। এই বিষয়ে বিরোধীদলীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ফ্লোর নিয়ে কথা বলতে চাইলে স্পিকার তাকে সুযোগ দেননি। তারপরও সুরঞ্জিত বলেন, ‘রাজ্জাক ভূঁইয়া সাহেব যে সংশোধনী এনেছেন তাতে মনে এ প্রশ্ন জাগে যে, বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়া ভারতের কেউ বাস করছে। বাঙালি বলতে এইটুকু বোঝায় যে, যারা বাংলা ভাষা বলে।’ সুরঞ্জিত এটুকু বলার পরে স্পিকার তাকে বসতে বলেন এবং প্রস্তাবটি ভোটে দেন। কণ্ঠ ভোটে সংশোধনী প্রস্তাবটি পাস হয়ে যায় এবং বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলে পরিচিত হবেনÑ এই বিধানটি সংবিধানে যুক্ত হয়ে যায়। এর প্রতিবাদে মানবেন্দ্র লারমা পরিষদ থেকে ওয়াকআউট করেন।
রণাঙ্গনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ১৯৭১
এদিন এই ইস্যুতে সৈয়দ নজরুল ইসলামও বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ‘বাঙালি-পরিচয়ের প্রতিবাদে যাদের নাম করে এই পরিষদ-কক্ষ পরিত্যাগ করে চলে গেছেন, তারা বাঙালি জাতির অঙ্গ। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ৫ লক্ষ উপজাতি রয়েছে, তারা বাঙালি। তারা সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অঙ্গ বলে আমরা মনে করি। বাবু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেছেন। তিনি বলেছিলেন, তিনি বাংলা বলতে দ্বিধাবোধ করেন না। এ কথা স্বীকার করার পরেও কেন তিনি চলে গেলেন, তা যদি তিনি বলতেন, তাহলে আমি এই পরিষদে তার জবাব দিতে পারতাম। তার অনুপস্থিতিতে বলছি বলে এ কথা আমাকে বলতে হচ্ছে। ঐ পার্বত্য চট্টগ্রামের যারা অধিবাসী, তারা এই স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রেরই অঙ্গ। আমরা চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিকরা সারা বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণির নাগরিকের সমমর্যাদাসম্পন্ন হবে। তা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫ লক্ষ অধিবাসী বাঙালি জাতির গর্ব হিসেবে থাকবে। ত্রিশ লক্ষ বাঙালি প্রাণ দিয়েছে। সেই অধিকারের সংগ্রামে এবং সেই সংগ্রামের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যে একাত্মতা অনুভব করে নাই, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।’ (গণপরিষদ বিতর্ক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৯)।
প্রসঙ্গত, সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদে এই সংশোধনী পাসের কয়েকদিন আগে ১৯৭২ সালের ২৬ অক্টোবর গণপরিষদে খসড়া সংবিধানের ওপর আলোচনায় সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য এ এইচ এম কামারুজ্জামান বলেন, ‘আমার পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাইরাও অধিকার পাবেন। কোনো অংশ হতেই তারা বঞ্চিত হবেন না। বাঙালি হিসেবে আমরা বেঁচে থাকব। একটা জাতির অভ্যন্তরে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে বৈচিত্র্য অনেক বেশি, মাধুর্য অনেক বেশি। এই বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যে শুধু এক জাতি, এক কৃষ্টি, এক সংস্কৃতিÑ তা নয়। বহু অঞ্চলে বহু মানুষ আছে, তাদের নিজস্ব অনেক কিছু আছে। শত বৈচিত্র্য নিয়ে আমরা আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকব। কিন্তু সর্বোপরি থাকবে আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদ। সেই জাতীয়তাবাদ অক্ষুণ্ন রেখে সেই জাতির অভ্যন্তরের প্রতিটি মানুষের প্রতি আমরা সম-দৃষ্টি রেখে আমাদের জাতীয়তাবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করব।’
তার মানে আব্দুর রাজ্জাক ভূঁইয়া বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলে বিবেচিত হবেন বলে সংশোধনী প্রস্তাব আনলেও এটি যে বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের চিন্তায় আগে থেকেই ছিল সেটি কামারুজ্জামান ও সৈয়দ নজরুলের মতো নেতাদের বক্তৃতায় স্পষ্ট। কেননা সংশোধনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ড. কামাল হোসেনও এটি মেনে নেন। এই ইস্যুতে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত কথা বলতে চাইলেও স্পিকার তাকে সময় দেননি। এমনকি স্পিকার নিজেই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি কি বাঙালি হতে চান না?’ তাছাড়া জাতীয়তাবাদ (বাঙালি) যে সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি হবে, সেটি সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের আগেই ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে দেওয়া ভাষণে ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যে সমাবেশে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উপস্থিত ছিলেন। (সময়রেখায় বঙ্গবন্ধু, শিলালিপি/২০২১, পৃ. ২৩৩)। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলে পরিচিত হবেনÑ এই বিধানটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কেন শুরুতেই উল্লেখ করল না? কেন এটি একজন সদস্যের সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে পাস করতে হলো?
বিতর্ক যা-ই থাক, এ বিষয়ে ড. আনিসুজ্জামানের ভাষ্য: ‘পাহাড়ি জনসমষ্টির স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি সেদিন আমরা বুঝতে পারিনি। মানবেন্দ্র লারমাও সেদিন পাহাড়ি ও চাকমা প্রায় সমার্থক করে ফেলেছিলেন, অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করেননি। পাহাড়িদের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য যে সেদিন আমরা উপলব্ধি করতে সমর্থ হইনি, এ ছিল নিজেদের বড়ো রকম এক ব্যর্থতা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে প্রেরণা পেয়েও যে পাহাড়ি জাতীয়তাবোধের বা চাকমা জাতীয়তাবোধের সূচনা হতে পারে, এ-কথা একবারও আমাদের মনে হয়নি। নিজেদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাফল্যে আমরা তখন বেশিদূর দেখতে পারছি না, মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরে অন্য কোনো জাতীয়তাবোধ স্বীকার করতে পারছি না, বরঞ্চ তাকে সন্দেহের চোখে দেখছি। ৬ অনুচ্ছেদের ওই ছোট্ট সংশোধনীকে উপলক্ষ্য করে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জাতিত্বের সঙ্গে পাহাড়িদের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার যে-বিরোধ সেদিন সূচিত হলো, তার ফল কত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল, তা এখন আমরা জানি। (বিপুলা পৃথিবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯)।
গণপরিষদের বিতর্ক কতটা প্রাণবন্ত ছিল?
খসড়া সংবিধান বা সংবিধান বিলের ওপর সাধারণ আলোচনা চলে ১৯৭২ সালের ১৯ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত। ৮ কার্যদিবসে ১০টি বৈঠকে মোট ৩২ ঘণ্টা আলোচনা হয়। সে সময়কার ৪০৪ জন গণপরিষদ সদস্যের মধ্যে মাত্র ৪৮ জন সাধারণ আলোচনায় অংশ নেন। তাদের মধ্যে ৪৫ জন ছিলেন সরকারি দল আওয়ামী লীগের, একজন বিরোধী দল ন্যাপের (সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত) এবং দুজন স্বতন্ত্র সদস্য।
গণপরিষদ বিতর্কে অংশ নেওয়া ৪৮ জনের মধ্যে ১৬ জন খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন। সাতজন নারী সদস্যের মধ্যে চারজন সাধারণ আলোচনায় অংশ নেন। আওয়ামী লীগের ১৭৫ জন সদস্য বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ চেয়ে চিফ হুইপের কাছে নাম জমা দিয়েছিলেন, কিন্তু বেশির ভাগই সুযোগ পাননি।
বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ
সিলেট-২১ থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আবদুল আজিজ চৌধুরী এমন অভিযোগও করেছেন যে, সদস্যদের পরিষদ থেকে বের করে দেওয়ার হুমকির কারণে তারা প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজস্ব মতামত এ পরিষদে ব্যক্ত করতে পারছেন না। ১৯৭২ সালের ৩০ অক্টোবর তিনি গণপরিষদে দেওয়া বক্তব্যে ২৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ‘পূর্বদেশ’ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার একটি খবরের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, দ্বিতীয় তালিকার মাধ্যমে আরও কিছু আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যকে বাহির করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এর পূর্বে আওয়ামী লীগ দলীয় পরিষদ-সদস্যদের মধ্য হতে ২২ তারিখে ১৯ জনকে বাহির করেও দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অধিবেশন বসেছে। তাই আমি বলতে চাই, সদস্যদের বাহির করে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার ফলে এই মহান পরিষদের মাননীয় সদস্যদের ওপর প্রভাব পড়েছে। তাঁরা প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজস্ব মতামত এই পরিষদে ব্যক্ত করতে পারেননি। এই পরিষদ যে প্রভাবান্বিত হয়েছে মতামত প্রকাশের ব্যাপারে, সে সম্পর্কে দেশবাসী নিশ্চিতÑ এই আমার বক্তব্য। (গণপরিষদ বিতর্ক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৫)।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক আসিফ নজরুল মনে করেন, সংবিধান বিষয়ে জনগণের মতামত নেওয়া হয়েছিল সীমিতভাবে। খসড়া প্রণয়নের পর কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনাও করা হয়নি। ১৯৭০ সালের নির্বাচন বর্জন করার কারণে ভাসানী ন্যাপের মতো দেশের একটি বড়ো রাজনৈতিক দলের গণপরিষদে কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না। আবার ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকা পালনের কারণে জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামিক দলগুলোর সংবিধান প্রশ্নে মতামত দেওয়ারই সুযোগ ছিল না, যদিও তাদের সদস্য ও সমর্থকদের ভোটাধিকার অব্যাহত ছিল। (আসিফ নজরুল, সংবিধান বিতর্ক ১৯৭২, প্রথমা/২০২২, পৃ. ৪০)।
তবে অস্বীকার করার উপায় নেই, নানা সীমাবদ্ধতার পরও গণপরিষদের বিতর্ক ছিল প্রাণবন্ত, বিশদ ও জ্ঞানগর্ভ। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত অবাধে কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন এবং গণপরিষদের বাইরের এমন কোনো বিতর্ক ছিল না, যা তিনি গণপরিষদে উত্থাপন করেননি। প্রতিটি বিষয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে তিনি সংবিধানের বিভিন্ন বিধিবিধানের পেছনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে সরকারপক্ষকে বাধ্য করেছেন।
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাও অনেক বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আবদুল আজিজ চৌধুরী এবং অনেক ক্ষেত্রে সংবিধানে খসড়া প্রণয়ন কমিটির সদস্য আছাদুজ্জামান খানও বিভিন্ন সময়ে সাহসের সঙ্গে বক্তব্য রেখেছেন। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও সংবিধান প্রণয়ন বিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত উত্তর দিয়েছেন। ফলে কার বক্তব্য কিংবা কার সংশোধনী কতটুকু গ্রহণ করা হলো, সেই বিতর্কের বাইরে গিয়েও এটা বলা যায় যে, সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় গণপরিষদ বেশ প্রাণবন্তই ছিল এবং নানা সীমাবদ্ধতার পরও এখানের আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ককে পার্লামেন্টারি ডিবেটের একটা শুভ সূচনা বলা যেতে পারে।
দ্বিতীয় অধ্যায়
সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের প্রেক্ষাপট,
ভীতি ও বাস্তবতা
সংসদ সদস্য পদ বাতিলসম্পর্কিত সংবিধানের যে ৭০ অনুচ্ছেদ নিয়ে এখনো বিতর্ক হয় এবং যে বিধানকে সংসদ সদস্যদের কথা বলা তথা তাদের স্বাধীন মত প্রকাশের পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা বলে মনে করা হয়, সেই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয় ১৯৭২ সালে গণপরিষদ গঠনকালেই।
১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ ‘বাংলাদেশ কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি মেম্বারস অর্ডার’ নামে যে আইনটি করা হয়, সেখানে বলা হয়, গণপরিষদের যে সদস্য নিজ দল থেকে পদত্যাগ করবেন বা নিজ দল থেকে বহিষ্কৃত হবেন, তিনি আর পরিষদের সদস্য হিসেবে থাকতে পারবেন না। তবে এই আদেশের বিধান অনুযায়ী গণপরিষদের সদস্যপদ হারানো কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কোনো আইন অনুযায়ী অযোগ্য না হন তাহলে তিনি গণপরিষদের শূন্য আসনে নির্বাচনে প্রার্থী হতে অযোগ্য বলে গণ্য হবেন না। এই আদেশের অধীনে গৃহীত কোনো আদেশ বা কার্যক্রমকে কোনো আদালত প্রশ্ন করতে পারবে না। এই আদেশের প্রস্তাবনায় বলা হয়, যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকর ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল, তাই তা নিশ্চিত করার জন্য আইনটি করা হয়েছে।
বাহাত্তর সালেই আপত্তি
১৯৭২ সালে সংবিধান বিলের ৭০ অনুচ্ছেদেও এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হলে এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যাপক আবু সাইয়িদ বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুকে সংসদ সদস্যদের পদ বাতিল সম্পর্কিত ৭০ অনুচ্ছেদ নিয়ে নিজের অবস্থান তুলে ধরে বললাম, অন্য দেশের সংবিধানে এমনটি নেই। পরে ৭০ অনুচ্ছেদ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমরা আরো কয়েকজন আলোচনা করি। কিন্তু তিনি বললেন, এদেশের মানুষকে আমি জানি। অনেকেই লোভে পড়ে ব্যক্তি স্বার্থে এদিক ওদিক করে। সুষ্ঠুভাবে দেশ চালাতে গেলে গণতন্ত্রের সঙ্গে স্থিতিশীল সরকার দরকার।’
কমিটির জ্যেষ্ঠতম সদস্য হাফেজ হাবীবুর রহমানও (১৯১৫-১৯৮৯) ৭০ অনুচ্ছেদ নিয়ে নিজের আপত্তির কথা জানান। তিনি এ বিষয়ে সংবিধান বিলের সঙ্গে নোট অব ডিসেন্ট দেন। শুধু তিনি একা নন, সংবিধান প্রণয়ন কমিটির আরও চারজন সদস্য (আসাদুজ্জামান খান, এ কে মোশাররফ হোসেন আকন্দ, আব্দুল মুন্তাকীম চৌধুরী ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত) ৭০ অনুচ্ছেদের বিরোধিতা করেন।
হাফেজ হাবীবুর রহমান বলেন, ‘গণতান্ত্রিক বিশ্বের কোথাও কোনো রাজনৈতিক দল থেকে বহিষ্কারের কারণে সংসদের সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায় না। সংসদ সদস্য পদের এই ধরনের অবসান কেবল একটি স্বৈরাচারী শাসনে পাওয়া যায়, যেখানে একদলীয় শাসনব্যবস্থা বিরাজ করে। একজন সংসদ সদস্য ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হন, দলের সদস্যদের দ্বারা নন। একবার তিনি নির্বাচিত হলে তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য হন এবং তখন তিনি কেবল তাঁর রাজনৈতিক দলের সদস্য থাকেন না। সদস্য পদ বাতিলের এ ধরনের ব্যবস্থার ফলে দলীয় একনায়কত্ব এবং দলের নেতার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা পায়।’
হাফেজ হাবীবুর রহমানের মতে, কোনো দলের কখনই জনগণের রায় অর্থাৎ নির্বাচন বাতিল করার অধিকার থাকতে পারে না। দলের নেতারা যেখানে তাঁদের রাজনৈতিক আচরণের জন্য ভোটারদের কাছে দায়বদ্ধ নন, সেখানে একজন সংসদ সদস্য তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ভোটারদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য।
![]()




 Hello, Sign in
Hello, Sign in 
 Cart
Cart