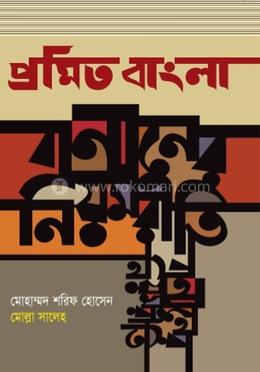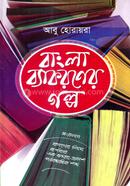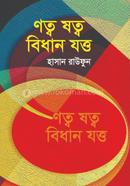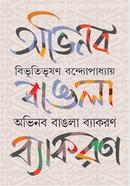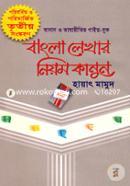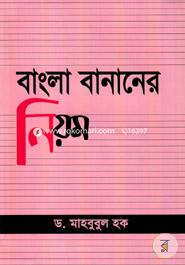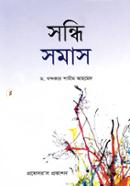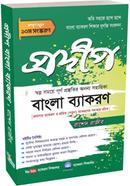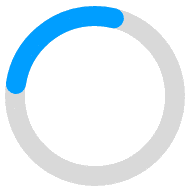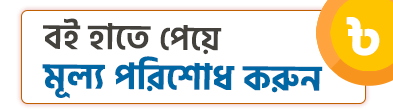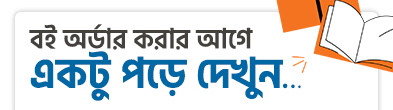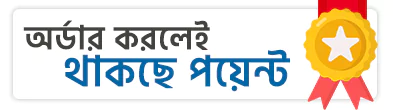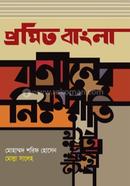শব্দের বানান ও উচ্চারণ শুদ্ধ না হলে ভাষার সৌন্দর্য ও শ্রী বৃদ্ধি হয় না। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এ কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। শুদ্ধ বানান ও উচ্চারণের জন্য বাংলা ভাষা এ যাবৎকাল সমালোচিত হয়ে আসছে।
জটিল বর্ণমালা, শব্দগঠন ও উচ্চারণ দুরূহ বাংলা ভাষার সম্পর্কে এমন একটা কথা প্রচলিত। কেননা কোনো ভাষায়ই নিরঙ্কুশ ত্রুটিপূর্ণ নয়। বাংলা শব্দের বানান ও উচ্চারণে রয়েছে নানান সমস্যা। মধ্যযুগের অন্তিম পর্বে এসে মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহারের পর থেকে শুরু হয় বর্ণমালা ও বানান সংস্কারের পালা। বর্ণ ও বানান অভিন্ন নয় কিন্তু তাদের মধ্যে সম্পর্ক গভীর। কারণ, বানান বিন্যস্ত হয় বর্ণ দ্বারাই। বর্ণের আকৃতি যেমন-বানান অক্ষুণ্ণ রেখেই বদলে যেতে পারে, তেমনি বর্ণ রূপ অপরিবর্তিত রেখেও বদলে দেওয়া যায় শব্দের বানান। মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের আগে নানাজন নানা বর্ণবিন্যাসে ও বানানে লিখতেন। বানানের ব্যাপারে তারা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী। ফলে বিচিত্র রকম ছিল বর্ণের আকৃতি। নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ১৭৭৮ সালে প্রথম বাংলা বর্ণমালা ঢালাই করেন ধাতুতে।
এরপর শুরু হয় যুগান্তর। তারপর অজস্র বই মুদ্রিত হয় নানা আকৃতির বর্ণে ও বিচিত্র বানানে।
সুতরাং অচিরেই প্রয়োজন দেখা দেয় 'সুস্থিত' মান ভাষা লেখা ও মুদ্রণের জন্য 'সুস্থিত' বর্ণমালা ও বানান। উনিশ শতকেই যেমন-বাংলা ভাষার মানরূপ দেওয়ার চেষ্টা চলে, তেমনি প্রয়াস চলে বাংলা বর্ণ ও বানানের মানরূপ প্রতিষ্ঠার। সক্রিয় হয়ে ওঠেন সংস্কারবাদী পণ্ডিতের দল। একদল সংস্কারক মুদ্রাকরের দৃষ্টিতে
সংস্কার করতে চেয়েছেন বর্ণমালা ও বানান। আরেক দল চেয়েছেন ব্যুৎপত্তি অনুসারে বাংলা বানানের রূপ স্থির করতে। ফলে বানান হয়ে উঠল একদিকে বেশি গোঁড়ামিযুক্ত অপরদিকে অতিবৈজ্ঞানিক। এই দুয়ের কোনোটাই বাংলা ভাষার জন্য সহনীয় ছিল না। (হুমায়ুন আজাদ: বাংলা ভাষা, ১ম খণ্ড)
আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধু ভাষায় বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ শতকরা মোটামুটি ৪৪ ভাগ। এছাড়া রয়েছে তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশি এবং বিদেশি অজস্র শব্দ। বাংলায় এখন প্রায় আড়াই হাজার আরবি-ফারসি শব্দ প্রচলিত আছে। প্রায় পঁয়ত্রিশটি তুর্কি শব্দ, শ'খানেক পর্তুগিজ শব্দ এবং প্রায় এক হাজার ইংরেজি শব্দ বাংলায় প্রচলিত এবং বেড়েই চলেছে এই শব্দ সংখ্যা। এর ফলে ব্যুৎপত্তিগত এবং উচ্চারণগত দিক থেকে বাংলা বানান বা বর্ণবিন্যাস রীতিতে ক্রমেই একটা ভ্রান্তির বিষয় সবার জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে (নরেন বিশ্বাস- প্রসঙ্গা-বাঙলা ভাষা)। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ-এর ভাষায়-"আমাদের মনে হয় উচ্চারণ অনুযায়ী বানান পরিবর্তন হলে 'প্রাকৃত বাংলায়' তৎসম শব্দ হাজারেও একটা থাকবে না, নতুন বাংলা ভাষার সৃষ্টি হবে।" রবীন্দ্রনাথও এ কথা অন্য প্রসতো স্বীকার করেছেন-"বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই দেখা যাবে বাংলায় তৎসম শব্দ নেই বললেই হয়। এমনকি কোনো নতুন সংস্কৃত শব্দ আমদানি করলে বাংলার নিয়মে তখনি সেটা প্রাকৃত রূপ ধরবে। ফলে আমরা লিখি এক আর পড়ি আর এক। অর্থাৎ আমরা লিখি সংস্কৃত ভাষায়, আর ঠিক সেটাই পড়ি প্রাকৃত বাংলা ভাষায়।” উল্লেখ্য কবি এখানে 'প্রাকৃত বাংলা' বলতে প্রকৃতপক্ষে 'প্রাকৃতজনের' কথ্য ভাষা বা লৌকিক বাংলাকে বুঝিয়েছেন।
বাংলা ভাষার বানান ও উচ্চারণের এই বেহাল দশার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান সংস্কার সমিতি' নামে একটি কমিটি গঠন করেন। ওই সমিতি ১৯৩৭ সালের জুন মাসে বানান সংস্কারের একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ওই পুস্তকের ভূমিকায় উপাচার্য লেখেন (১৯৩৬, ৮ মে)- 'বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দসমূহের মধ্যে যেগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে অপরিবর্তিতভাকে আসিয়াছে তাহাদের বানান প্রায় সুনির্দিষ্ট। কিন্তু যে সকল শব্দ সংস্কৃত নহে, অর্থাৎ যেগুলি দেশজ বা অজ্ঞাত মূল, বিদেশাগত অথবা সংস্কৃত বা বিদেশি শব্দের অপভ্রংশ, তাহাদের বানানে বহুস্থলে বিভিন্নতা দেখা যায়। ইহার ফলে লেখক, পাঠক, শিক্ষক ও ছাত্র সকলকেই কিছু কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বাঙলা বানানের একটা বহুজন গ্রাহ্য নিয়ম দশ-বিশ বৎসরের মধ্যে যে আপন হইতেই গড়িয়া উঠিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।...'
![]()




 Hello, Sign in
Hello, Sign in 
 Cart
Cart