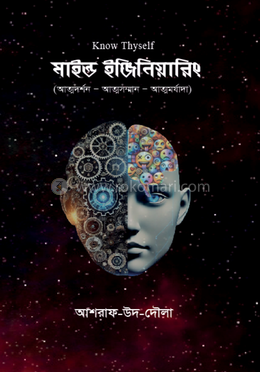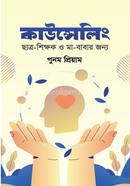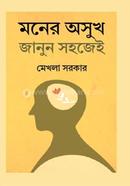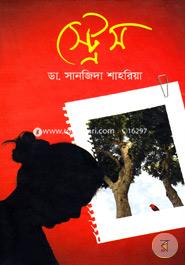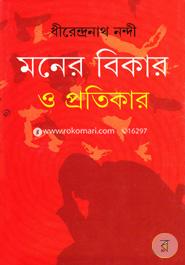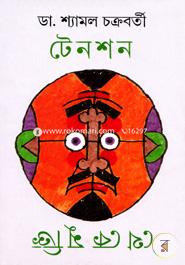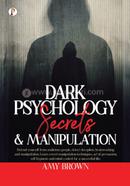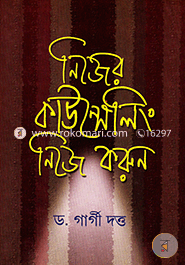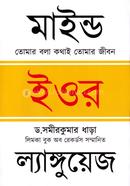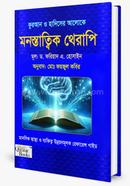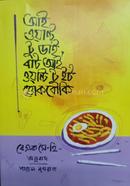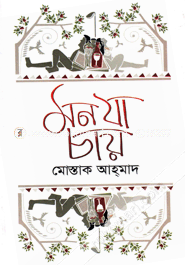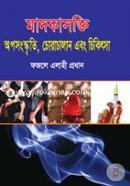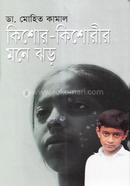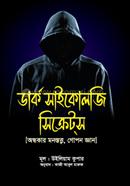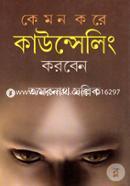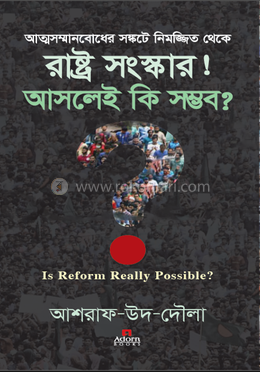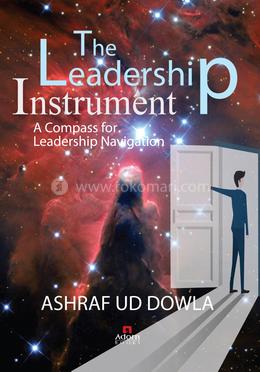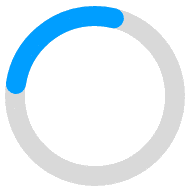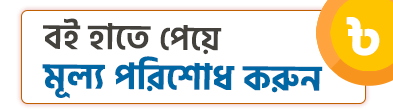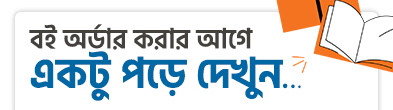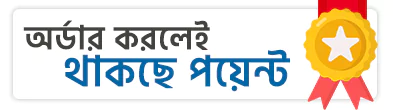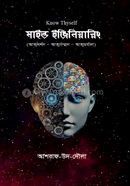প্রথম অধ্যায়
Know Thyself
মাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
১ দর্শন ও ধর্ম বিশ্বাসে হৃদয়ের পরিচয়
আমি কে, কোথা থেকে এলাম, কী আমার আত্মার পরিচয়Ñএসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেতে জ্ঞানী, গুণী, ঋষি আর সাধকগণ তপস্যা করে চলেছেন সেই প্রাচীন কাল থেকে। তাঁদের মতে, আপাত ক্ষুদ্র এই প্রশ্নটির মাঝেই গুপ্তধনের মতো সুপ্ত হয়ে লুকিয়ে রয়েছে মহাবিশ্বের সব অমীমাংসিত প্রশ্নের সমাধান, আর তাই প্রশ্নটি নিতান্ত কোনো সহজ আর হেলাফেলার নয়। ব¯‘ত, এমন প্রশ্ন করার আগে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে যে, আপনি সত্যিই এই জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছেন যথাসম্ভব সবটুকু প্রচেষ্টা দিয়ে। মানুষের জীবনে যদি একটিমাত্র মৌলিক প্রশ্ন থেকে থাকে, তবে তা এই প্রশ্নটিই। ব¯‘ত, আপন সত্তা সম্পর্কে এমন মৌলিক প্রশ্নের উত্তর আপনি অন্য কারও থেকে শিখে নিতে বা জেনে নিতে পারবেন না, বরং তা নিজেকেই উদ্ধার করতে হবে। ফুসফুসে অক্সিজেন নেওয়ার কাজটি যেমন একান্তই আপনার, তেমনি ‘আমি কে’ এই প্রশ্নের উত্তর কঠোর অধ্যবসায় ও নিমগ্ন জ্ঞানসাধনা বলে কেবল নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। নিজেকে জানার পথে, আপন সত্তার প্রকৃত পরিচয় উপলব্ধির জগতে আপনার জন্য এটি একটি একান্ত ব্যক্তিগত ভ্রমণ।
ইসলাম ধর্মের মতে শারীরিক নয়, বরং আত্মিক মানুষই মানুষের পরিচয়; তবে প্রতিটি মানুষের মন বা আত্মার দুটি অংশ রয়েছে, যার একটি নফস আর অন্যটি রুহ। নফস মানব দেহের নানা ই”েছ, অনুভূতি, আকাক্সক্ষা আর শারীরবৃত্তীয় বিষয়ের সাথে যুক্ত, তাই শরীরের প্রয়োজনগুলোই নফসের চালিকাশক্তি। অন্যদিকে প্রতিটি মানুষের মাঝে উপ¯ি’ত রুহ হলো মহান স্রষ্টার স্বর্গীয় সৃষ্টি, যা শরীরের ওপর নির্ভর করে পৃথিবীতে শুধু পরিভ্রমণ করে চলেছে। শারীরিকভাবে জন্মগ্রহণের বহু পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছে অবিনশ্বর প্রতিটি রুহ এবং ক্রমান্বয়ে এক একটি মানব শরীরের মাধ্যমে তা দুনিয়াতে অবতরণ করে চলেছে। মুসলিমগণের বিশ্বাস, জগতে রুহগুলোকে এ কারণেই প্রেরণ করা হয়, যেন তারা স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারে আর মহান স্রষ্টা সেই রুহগুলোকে আনুগত্যের পরীক্ষায় মূল্যায়ন করে উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করতে পারেন। এই ধর্ম মতে, রুহসমূহ জগতে একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেহের ওপর অব¯’ান করে নিজ নিজ পরীক্ষা শেষে পরকালে পৌঁছে জান্নাতের আকাক্সক্ষায় এক মহাবিচার দিনের অপেক্ষা করতে থাকে।
খ্রিস্টধর্মের ব্যাখ্যায় আত্মাকে বলা হয়েছে, শারীরিক কাঠামোর বাইরে মহান স্রষ্টার স্বরূপ নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়া স্রষ্টারই অবিনশ্বর অংশ, তাই আত্মাই মানুষের চেতনা ও নৈতিকতার পটভূমি। খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসীরা বলেন, প্রতিটি মানুষের আত্মা আদি পাপ নিয়ে পৃথিবীতে আসে এবং কেবল যিশুখ্রিস্টকে বিশ্বাস করার মধ্য দিয়েই তারা সেই পাপ মুক্ত হয়ে স্রষ্টার সাথে পুনরায় মিলিত হওয়ার উপযুক্ত হয়। এই বিশ্বাস মতে, সকল আত্মা এক মহাবিচার দিনের মুখোমুখি হবে এবং সেদিন বিশ্বাস ও কর্মের বিচারে জান্নাত কিংবা জাহান্নামে ঠিকানা হবে তাদের।
হিন্দুশাস্ত্র মতে, আত্মা বিধাতার এক অবিনশ্বর অংশ, যা পৃথিবীতে এসে নানা প্রাণের মাঝে ঘুরেফিরে চলেছে মুক্তির প্রত্যাশায়। এই বিশ্বাস মতে, প্রতিটি প্রাণ তা হোক মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণী অথবা উদ্ভিদ, সকলের মাঝেই রয়েছে সর্বজনীন আত্মা এবং সেসব আত্মা নানা বেশে নানা প্রাণের মাঝে বিচরণ করে চলেছে জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে। এই বিশ্বাস মতে, সকল জীবের আত্মা একই স্বরূপ নিয়ে গঠিত, তাই তারা ঘুরেফিরে ভ্রমণ করে চলেছে কখনো মানুষের দেহে, কখনো কোনো গাছের কাণ্ডে আবার কখনো কোনো মাছের বা অন্য কোনো প্রাণীর জীবনে।
বৌদ্ধমতে, ‘আত্মা’ কোনো চির¯’ায়ী, অপরিবর্তনীয় সত্তার অস্তিত্ব নয়। বৌদ্ধ দর্শনে ‘অনাত্মা’ বা ‘নিরাত্মকতা’ ধারণায় বিশ্বাস করা হয়। এই বিশ্বাস মতে, ব্যক্তিগত সত্তা একটি সাময়িক ও পরিবর্তনশীল উপাদানের সমষ্টি যেখানে এখানে ‘অনাত্মা’ ধারণাটিই মূলভিত্তি। এর মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, কোনো ¯’ায়ী কিংবা স্বাধীন আত্মা বলে কিছু নেই, যা কোনো ব্যক্তিত্ব বা অস্তিত্বের কেন্দ্রে অব¯’ান করে। বৌদ্ধমতে, ব্যক্তি বা ‘আমি’ আসলে পঞ্চস্কন্ধের (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) সমন্বয়। এই মতে সবকিছুই অনিত্য, অর্থাৎ পরিবর্তনশীল। ব্যক্তিত্ব বা অস্তিত্ব কোনো একক আত্মার ওপর নির্ভর করে না বরং, এটি কার্যকারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। এই মতে নির্বাণ হলো চূড়ান্ত মুক্তি, যেখানে লিপ্সা (তৃষ্ণা), দ্বেষ এবং মোহের সমাপ্তি ঘটে। নির্বাণ কোনো চির¯’ায়ী আত্মার অব¯’ানে পৌঁছানো নয়, বরং দুঃখের সমাপ্তি। বুদ্ধ বলেননি যে আত্মা ধ্বংস হয়; তিনি বলেছেন আত্মার অস্তিত্বই নেই। এই দর্শনে আত্মার ধারণার অনুপ¯ি’তি সত্ত্বেও নৈতিক দায়বদ্ধতা এবং কর্মের ধারণা রয়েছে। এক জীবনের কর্ম অন্য জীবনের ওপর প্রভাব ফেলে, তবে তা কোনো চির¯’ায়ী আত্মার মাধ্যমে নয়, বরং কারণ এবং ফলাফলের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে ঘটে। বৌদ্ধমতে, পুনর্জন্ম একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যেখানে এক জীবনের কর্ম অন্য জীবনে ফলাফল বয়ে আনে।
মানুষের মন বা আত্মা নিয়ে প্রাচীন এবং আধুনিক দর্শন তত্ত্বে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ রয়েছে। প্রাচীন দর্শনগুলোতে আত্মা, মনের প্রকৃতি এবং চিন্তার সম্পর্ককে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, কিš‘ আধুনিক দর্শনে মন এবং মস্তিষ্কের সম্পর্ককে মনস্তাত্ত্বিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষিত হয়েছে। প্লেটো বিশ্বাস করতেন যে, মন তিনটি অংশে বিভক্তÑবুদ্ধি (জধঃরড়হধষ ঝড়ঁষ), ই”ছা (ঝঢ়রৎরঃবফ ঝড়ঁষ) এবং আবেগ (অঢ়ঢ়বঃরঃরাব ঝড়ঁষ)। অ্যারিস্টটল মনে করতেন, মন একপ্রকার অস্তিত্ব যা চিন্তা, অনুভূতি এবং মনোভাবের সাথে সম্পর্কিত। তার মতে, মন মানুষের অভ্যন্তরীণ জীবনের কেন্দ্রে অব¯’ান করে এবং এটি ব¯‘গত বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত।
আধুনিক মনস্তত্ত্বে মন ও মস্তিষ্কের সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছিলেন, ইড বা প্রাথমিক ই”ছা এবং আবেগ, ইগো যা বাস্তবতা মেনে চিন্তা এবং আচরণ করার মন, আর সুপার ইগো যা নৈতিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক নিয়ম মেনে চলার হৃদয় কাঠামো। ফ্রয়েডের মতে, মানুষের মন অনেক গভীর এবং অচেতন স্তরে কাজ করে, যা সাধারণত মানুষের চিন্তাভাবনার বাইরে অব¯’ান করে। তিনি বলেছেন, মানুষ তার অচেতন মন থেকে প্রভাবিত হয় এবং সেই প্রভাব তার আচরণে প্রতিফলিত হয়। আধুনিক যুগে বিহেভিওরিজম মনোবিদ্যায় মন ও আচরণকে মূলত পরিবর্তনশীল পরিবেশ এবং প্রতিক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিহেভিওরিস্টরা মনে করেন ‘মন’ একটি দৃশ্যমান বাস্তব আচরণের সমষ্টি, তবে চিন্তা বা অভ্যন্তরীণ অনুভূতির বিষয়টি অগোচর। জন বিওয়াটসন এবং বি.এফ. স্কিনার বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের মন ও অনুভূতি শুধু পরিবেশের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই প্রমাণিত হতে পারে, তাই চিন্তা বা আবেগের পরিবর্তে আচরণকেই বিজ্ঞানগতভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত। অন্যদিকে কগনিটিভ মনোবিজ্ঞান মনের প্রকৃতিকে তথ্য প্রসেসিং মডেল হিসেবে দেখে। এই ব্যাখ্যা মানব মনের চিন্তা, অনুভূতি, মনে রাখা, সমস্যা সমাধান ইত্যাদির সাথে হৃদয়কে সম্পর্কিত করে। কগনিটিভ দর্শন মতে, মন হলো একটি ‘কম্পিউটার’, যার মধ্যে তথ্যপ্রক্রিয়াকরণ এবং তা বিশ্লেষণ করা হয়। জেরমি বেন্টাম ও নোয়াম চমস্কি মনে করতেন যে মানুষের মন তথ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে তার অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা বুঝে আচরণ তৈরি করে।
আধুনিক যুগে নিউরোসায়েন্স এবং ব্রেন সায়েন্স মন ও মস্তিষ্কের সম্পর্ক নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করে চলেছে। এখানে মনে করা হয় যে, মানুষের চিন্তা ও অনুভূতি সম্পূর্ণভাবে মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র এবং নিউরনের কার্যকলাপের ওপর নির্ভরশীল। এই মতে, মন হলো একটি স্নায়বিক এবং বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া, যা মস্তিষ্কের মধ্যে প্রতিনিয়ত সচল।
![]()



 Hello, Sign in
Hello, Sign in  Cart
Cart