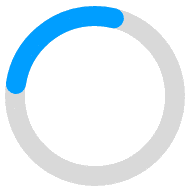গোড়ার কথা
একত্ববাদী বলে পরিচিত তিনটি ধর্মেরই নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। যাঁরা বিশ্বাসীÑ তাঁরা ইহুদি, খ্রিষ্টান অথবা মুসলমান যা-ই হোন না কেন, এসব সংকলিত দলিল তথা ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে তাঁদের বিশ্বাসের বুনিয়াদ। তাঁদের কাছে এসব ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে সে ধরনের আসমানি ওহির লিপিবদ্ধ রূপ, যে ধরনের ওহি হজরত ইবরাহিম (আ.) এবং হজরত মুসা (আ.) সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছিলেন এবং যে ওহি হজরত ঈসা (আ.) লাভ করেছিলেন ফাদার বা পিতার নামে। আর হজরত মোহাম্মদ (স.) লাভ করেছিলেন প্রধান ফেরেশতা জিব্রাঈলের মাধ্যমে।
ধর্মীয় ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে তাওরাত,* জবুর, ইঞ্জিল (অর্থাৎ বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম) এবং কোরআন একই ধরনের ওহি বা প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ধর্মগ্রন্থ। মুসলমানেরা যদিও এ নীতি মেনে চলেন, কিন্তু পাশ্চাত্যের ইহুদি-খ্রিষ্টান সংখ্যাগুরু সমাজ কোরআনকে প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ধর্মগ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করতে চান না। পরস্পরের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে এই যে দৃষ্টিভঙ্গি, খুব সম্ভব এর থেকেই বোঝা যাবে যে, একটি ধর্মীয় সমাজ অপর ধর্মীয় সমাজ সম্পর্কে কী ধরনের মনোভাব পোষণ করেন।
হিব্রু ভাষার বাইবেল হলো ইহুদিদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ। উল্লেখ্য যে, হিব্রু বাইবেল খ্রিষ্টানদের বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত ওল্ড টেস্টামেন্ট বা পুরাতন নিয়ম থেকে কিছুটা আমাদের খ্রিষ্টানরা এই ওল্ড টেস্টামেন্টে এমন বেশ কয়েকটি অধ্যায় সংযোজিত করেছেন যা হিব্রু বাইবেলে নেই। এ সংযোজনা কিন্তু বাস্তবে ইহুদি মতবাদে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে বলে মনে হয় না। কেননা, নিজস্ব হিব্রু বাইবেলের পরে আর কোনো ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ার কথা ইহুদিরা স্বীকার করেন না।
খ্রিষ্টানরা হিব্রু বাইবেল যেমনটি ছিল তেমনিভাবে সেটিকে গ্রহণ করেছেন এবং তার সাথে আরও কিছু অধ্যায় সংযুক্ত করে নিয়েছেন। অন্যদিকে খ্রিস্টানরা নিজেরাও কিন্তু যিশুর (হজরত ঈসার) ধর্মপ্রচারের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং মানুষের কাছে পরিচিত সবকটি রচনাকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেননি। যিশুর জীবনী ও শিক্ষাসংক্রান্ত পুস্তকের সংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু গির্জার পুরোহিত-অধিকারীরা এসব থেকে যাচাই-বাছাই ও কাটছাঁট করে মাত্র কতিপয় রচনাকে নিজেদের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন। এভাবে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে মাত্র কিছুসংখ্যক রচনা স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ‘প্রামাণ্য’ বলে পরিচিত চারটি গসপেল বা সুসমাচার। খ্রিষ্টানরাও যিশু এবং তাঁর প্রেরিতদের পর আর কোনো প্রত্যাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সে কারণে কোরআন তাঁদের কাছে ‘বাতিল’ বলে গণ্য।
কোরআনের বাণীসমূহ অবতীর্ণ হয় যিশুখ্রিষ্টের ছয়শ বছর পর। তাওরাত ও গসপেলের (ইঞ্জিল) বহু তথ্য ও পরিসংখ্যানের উল্লেখ ছাড়াও কোরআনে তাওরাত ও ইঞ্জিলের বহুল উদ্ধৃতি বিদ্যমান। কোরআন ইতঃপূর্বেকার সবকটি আসমানি কিতাবের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে (সুরা ৪, আয়াত ১৩৬)। এ ছাড়াও কোরআন অন্যান্য পয়গম্বর যেমন : যিশু বা হজরত ঈসা, হজরত মুসা ও তাঁর পরবর্তী নবিদের* এবং তাঁদের ওপরে নাজিলকৃত আল্লাহর বাণী সম্পর্কে সবিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। বাইবেলের মতো কোরআনও তাঁর জন্মকে একটি অতি-প্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছে। যিশুমাতা মেরি বা হজরত মরিয়মকেও কোরআনে বিশেষ মর্যাদার আসন দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে কোরআনের ১৯নং সুরার।
উপরে বর্ণিত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে পাশ্চাত্যের লোকজনের অজ্ঞাত। এতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছুই নেই। কেননা পাশ্চাত্য জগতে পুরুষাণুক্রমে এমনভাবে এ শিক্ষাই দিয়ে আসা হচ্ছে যে, ধর্মীয় সমস্যাই মানবতার প্রধান প্রতিবন্ধক; আর যে ধর্মটি স্বীয় ‘অজ্ঞানতার’ দ্বারা বহুলভাবে এ সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে, তা হলো ইসলাম। এক্ষেত্রে ‘মোহামেডান রিলিজিয়ন’ এবং ‘মোহামেডান্স’ এ টার্ম দুটি হাতিয়ার হিসেবে কম ব্যবহৃত হচ্ছে না। একটা ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাস থেকেই এই দুটি টার্ম বা বুলি আওড়ানো হয়।
যেমনÑইসলাম ধর্মটা সম্পূর্ণভাবে একজন মানুষের সৃষ্টি এবং এ ধর্মের প্রবর্তনায় গড বা বিধাতার (খ্রিষ্টীয় অর্থে) কোনো ভূমিকা নেই। অধুনা বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ইসলামের দার্শনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তাঁরাও কখনো ইসলামের ওহি বা প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বাণী সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের তেমন কোনো গরজ অনুভব করেন না। অথচ তা করা তাদের উচিত ছিল।
খ্রিষ্টানদের কোনো কোনো মহল মুসলমানদের কী ঘৃণার চোখেই না দেখে থাকেন। এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তখন, যখন আমি বাইবেল ও কোরআনের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের ব্যাপারে ওসব মহলের সাথে মতবিনিময়ের প্রয়াস চালিয়েছিলাম। চিরাচরিত পদ্ধতিতেই তাঁরা এ ব্যাপারে তাঁদের অনীহা প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে কোরআনের যে বক্তব্য, তা গ্রহণ করা তো দূরে থাক, এতদসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে কোরআনের প্রতি সামান্য আকার-ইঙ্গিতও তাঁরা বরদাশত করতে রাজি হননি। তাঁদের কাছে কোরআনের কোনো উদ্ধৃতি দেওয়াটা যেন শয়তানের বরাত দিয়ে কোনো কথা বলার শামিল!
যাহোক, অধুনা খ্রিষ্টান জগতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এ বিষয়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। ভাটিক্যানেরÑ‘নন-ক্রিশ্চিয়ান অ্যাফেয়ার্স’ দফতর দ্বিতীয় ভাটিক্যান কাউন্সিলের পর একটা তথ্যমূলক পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। এর ফরাসি নাম হচ্ছে ‘মুসলিম-খ্রিস্টান আলাপ-আলোচনার দিক-নির্দেশিকা’। প্রকাশক, অ্যানকোরা, রোম। ১৯৭০ সালে ফরাসি ভাষায় এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।
মুসলমানদের ব্যাপারে ভ্যাটিকানের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, এ পুস্তকে তার পরিচয় মেলে। এ পুস্তকে ইসলাম সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের প্রতি ‘অতীত থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় ধারণা ও কুসংস্কার এবং বিদ্বেষপ্রসূত বিকৃত মতামত’ পরিহারের আহ্বান জানানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভাটিক্যান থেকে সম্প্রচারিত এ দলিলে স্বীকার করা হয় যে, ‘অতীতে মুসলমানদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে এবং সেজন্য খ্রিস্টবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত পাশ্চাত্য সমাজই দায়ী।’ এ ছাড়াও মুসলমানদের অদৃষ্টবাদ, ইসলামিক বিধি-বিধান, তাঁদের রক্ষণশীলতা ইত্যাদি সম্পর্কে খ্রিস্টানদের মধ্যে যেসব ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছেÑএ পুস্তকে তার সমালোচনা করা হয়েছে। পুস্তকে স্রষ্টার একত্বের ভিত্তিতে ঐক্য গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে কার্ডিনাল কোয়েনিং এক সরকারি বৈঠকে যোগদানের জন্য কায়রো শহরে গিয়ে আল-আজহার মুসলিম ইউনিভার্সিটির জামে মসজিদে এ ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর সেই আহ্বান শুনে শ্রোতারা অবাক হয়ে গিয়েছিল। এ পুস্তকে এ কথারও উল্লেখ আছে যে, ১৯৬৭ সালে ভ্যাটিকান দফতর থেকে রমজানের শেষে যথাযথ গুরুত্বসহকারে মুসলমানদের প্রতি পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের জন্য খ্রিষ্টানদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
রোমান ক্যাথলিক বিশ্বাস ও ইসলামের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে এ যে পদক্ষেপ, তা কিন্তু এখানেই থেমে থাকেনি। বরং পরবর্তীকালে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও যৌথ বৈঠকের মাধ্যমে তা আরো গতিশীল এবং আরো সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। অবশ্য সংবাদপত্র, রেডিও-টেলিভিশনসহ প্রচারমাধ্যমের সমূহ সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এসব ঘটনা তেমন কোনো প্রচার পায়নি।
ভ্যাটিকানের ‘নন-ক্রিশ্চিয়ান অ্যাফেয়ার্স’ দফতরের প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল পিগনেডোলি ১৯৭৪ সালের ২৪ এপ্রিল সরকারি সফরে সৌদি আরব যান এবং বাদশাহ ফয়সলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সংবাদটিও পত্র-পত্রিকায় তেমন কোনো প্রচার পায়নি। ফরাসি সংবাদপত্র লে’ মন্ডেতে এ সম্পর্কে কয়েক ছত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র (২৫ এপ্রিল, ১৯৭৪)। ওই সংবাদ থেকে জানা যায়, মহামান্য পোপ ৪র্থ পল ‘ইসলামি বিশ্বের প্রধানতম নেতা মহামান্য বাদশাহ ফয়সলের নিকট শ্রদ্ধাজ্ঞাপনপূর্বক এ মর্মে এক বাণী প্রেরণ করেছিলেন যে, তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন, এক আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে ইসলামি বিশ্ব ও খ্রিস্টান জগৎ ঐক্য গড়ে তুলতে পারে।’ অন্য কিছু না হোক, শুধু এ বাণীর মর্ম থেকেই ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করা সম্ভব।
এর মাস ছয়েক পরে ১৯৭৮ সালের অক্টোবর মাসে সৌদি আরবের গ্র্যান্ড উলেমা এক সরকারি সফরে ভ্যাটিকানে আসেন এবং পোপ তাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষ্যে খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে এক আলোচনা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ‘ইসলামে মানুষের সাংস্কৃতিক অধিকার’। ভ্যাটিকানের সংবাদপত্র ‘অবজারভেটর রোমানো’ ১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর প্রথম পৃষ্ঠায় এ ঐতিহাসিক বৈঠকের বিবরণ প্রকাশ করে। এর সমাপ্তি অধিবেশনে রোমের সাইনড অব বিশপ-বর্গ হাজির ছিলেন। কিন্তু এই সমাপ্তি অধিবেশনের সংবাদটি প্রথম অধিবেশনের সংবাদের চেয়ে অনেক ছোটো করে ছাপা হয়েছিল।
সৌদি আরবের গ্র্যান্ড উলেমাকে এরপর সংবর্ধনা জানান জেনেভাস্থ গির্জাসমূহের একুমেনিক্যাল কাউন্সিল এবং স্ট্রাসবুর্গের লর্ডবিশপ মহামতি এলচিংগার। বিশপ তাঁর উপস্থিতিতেই গ্র্যান্ড উলেমাকে গির্জাতে জোহরের নামাজ আদায় করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। অনুমান করা চলে যে, ধর্মীয় গুরুত্ব বিচার করে নয়, বরং বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনার বিবরণী হিসেবে সংবাদপত্রগুলোতে ওইসব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। কেননা, এসব ঘটনার মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো সম্পর্কে যাঁদেরই প্রশ্ন করেছি, দেখেছি, তাঁদের অনেকেই এর গুরুত্ব সম্পর্কে তেমন সচেতন নন।
ইসলাম সম্পর্কে পোপ ৪র্থ পলের এই যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি, তা নিঃসন্দেহে এ দুই ধর্মের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার পথে উল্লেখযোগ্য এক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। পোপ নিজেই এ ব্যাপারে বলেছিলেন যে, ‘এক আল্লাহর উপাসনার ভিত্তিতে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার ব্যাপারে এক সুগভীর বিশ্বাস তাঁকে পরিচালিত করেছিল।’ ক্যাথলিক চার্চের প্রধানের কাছ থেকে মুসলমানদের জন্য এরকম মানসিক ভাবাবেগের সত্যি প্রয়োজন রয়েছে। কেননা বেশির ভাগ খ্রিস্টানই বড়ো হয়ে থাকেন ইসলাম-বিরোধিতার বিদ্বেষপূর্ণ এক উদ্দীপনার মধ্যে। ফলে তাঁরা আদর্শের প্রশ্নে ইসলামের নামগন্ধ পর্যন্ত বরদাশত করতে রাজি হন না। ভ্যাটিকান থেকে প্রকাশিত উপরোক্ত পুস্তকে এ জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে একথাও স্বীকার করা হয়েছে যে, উপরিউক্ত বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের কারণেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম যে কী জিনিস, সে সম্পর্কে বেশির ভাগ খ্রিস্টান পুরোপুরি অজ্ঞ থেকে যান। একই কারণে ইসলামি-প্রত্যাদেশ সম্পর্কে তাঁদের ধারণাও হয়ে থাকে ভ্রান্তিপূর্ণ।
যাহোক, একত্ববাদী কোনো একটি ধর্মের প্রত্যাদেশ-সংক্রান্ত কোনো বিষয় যখন পর্যালোচিত হয়Ñতখন এ বিষয়ে অপর দুটি একত্ববাদী ধর্মের বক্তব্য কী, তার তুলনামূলক আলোচনাও এসে পড়ে স্বাভাবিকভাবেই। তাছাড়া যে-কোনো সমস্যার সার্বিক বিচার-পর্যালোচনা বিচ্ছিন্ন কোনো আলোচনার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। এ কারণে যেসব বিশেষ বিষয়ে ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের বক্তব্যের সাথে বিশ-শতকের বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধ রয়েছে বলে মনে করা হয়, সেসবের পর্যালোচনায়ও উপরোক্ত তিন ধর্মের কথা না এসে পারে না। এ প্রসঙ্গে এ সত্যও অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, বস্তুবাদের সুতীব্র অভিযানের মুখে উপরিউক্ত তিন ধর্মই আজ হুমকির সম্মুখীন। এ যখন অবস্থা, তখন পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের গুণে এ ধর্ম তিনটি আজ সহজেই সমবেতভাবে একটি সুদৃঢ় প্রতিরোধ-প্রাচীর গড়ে তুলতে পারে। বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরবিরোধী বলে যে ধারণা, তা ইহুদি ও খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত দেশগুলোতে যেমন, তেমনি মুসলিম বিশ্বেরও কোনো কোনো মহলে বেশ জোরদার। কেন এই অবস্থাÑসে প্রশ্নের সার্বিক জবাব খুঁজে পাওয়ার জন্য দীর্ঘতর আলোচনা প্রয়োজন। এই পুস্তকে আমি এতদসংক্রান্ত একটা বিষয়ের শুধু একটা দিকের ওপরেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াস পেয়েছি। আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হলো : আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যজ্ঞানের আলোকে আসমানি কিতাব বলে পরিচিত ধর্মগ্রন্থসমূহের বক্তব্য কতটা সঠিক?
কিন্তু এ পর্যালোচনা তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে অগ্রসর হওয়ার আগে একটা মৌলিক প্রশ্নের সদুত্তর আমাদের খুঁজে নিতে হবে। সে প্রশ্নটি হচ্ছে ধর্মগ্রন্থের লিপিবদ্ধ বাণীসমূহ কতটা নির্ভুল? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে যে অবস্থা এবং যে পরিবেশে এসব বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছিল, তা যেমন আমাদের পরীক্ষা করে নিতে হবে; তেমনি এও পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে যে, কার মাধ্যমে বা কোন পথে এসব বাণী আমাদের কাছে পৌঁছেছে। পাশ্চাত্য জগতে বাইবেলের সমালোচনামূলক গবেষণা একদম হালের ঘটনা। শত শত বছর ধরে সেখানকার মানুষ নতুন ও পুরাতন নিয়ম তথা বাইবেলকে যখন যে অবস্থায় পেয়েছে, তখন সে অবস্থায় তা গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত থেকেছে। এ ধর্মগ্রন্থ তারা যেমন ভক্তিভরে পাঠ করেছে, তেমনি টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করে সে গ্রন্থের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি স্খলনেরও প্রয়াস পেয়েছে। শুধু তাই নয়, ধর্মগ্রন্থের বিরুদ্ধে সামান্যতম সমালোচনাকেও তারা ‘পাপ’ বলে গণ্য করতে ছাড়েনি। এ বিষয়ে পুরোহিতেরা ছিলেন সব সময়ই এক ডিগ্রি ওপরে। কেননা, তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ বাইবেল ভালোভাবে জানার সুযোগ ছিল বেশি। পক্ষান্তরে, বেশির ভাগ সাধারণ মানুষ ধর্মীয় ভাষণ কিংবা বিভিন্ন উপাসনা উপলক্ষে বাইবেলের নির্বাচিত অংশের পাঠ শুনেই নিজেদের ধন্য মেনেছে।
![]()




 Hello, Sign in
Hello, Sign in 
 Cart
Cart